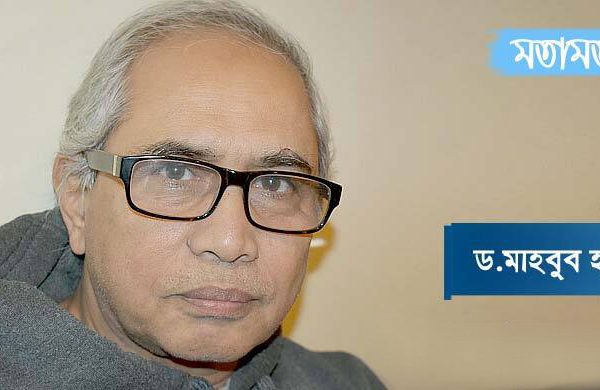তনুর মায়ের কষ্ট ও ঝুলে থাকা মামলার ভার
- আপডেট সময় বুধবার, ২০ মার্চ, ২০২৪, ৩.১৬ পিএম

শাহানা হুদা রঞ্জনা
একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা চালু থাকার পরও কেন মানুষ পুলিশ, প্রশাসন, বিচারব্যবস্থার ওপর ভরসা না রেখে শুধু আল্লাহর কাছে বিচার চাইছেন? এর পেছনে রয়েছে অসংখ্য কারণ। অধিকাংশ কারণ অলিখিতভাবে সমাজে গেড়ে বসেছে। আশির দশকের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত রুবেল, মোমেনা, নাদিম, প্রীতি, দীপন, তনু, অভিজিৎ সবার মৃত্যু এমন এক সুতোয় গাঁথা, যে সুতো বিচার না পাওয়ার সেই অলিখিত গল্প বলে। এদের সবার পরিবার বিছিন্নভাবে প্রশাসন, রাষ্ট্রব্যবস্থা ও বিচারব্যবস্থাকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছেন। অতীতে এরকম অনেক নিপীড়ন, নির্যাতন, ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের বিচার চেয়েও পাওয়া যায়নি বা বিচারের ফল নির্যাতিত মানুষের পক্ষে যায়নি। এখন বিচারপ্রার্থী মানুষ বলছেন, “আমরা বিচার চাই না” বা “আমরা আল্লাহর কাছে বিচার চাই”।
‘তনুকে হারানোর আট বছর শেষ। বিচারের কোনো লক্ষণ দেখি না। কত সাংবাদিক আসেন কত সাংবাদিক ফোন দেন। সবাই একই কথা জিজ্ঞেস করেন। অথচ মামলার তদন্তে কোনো অগ্রগতি নেই। আমরা আর কতভাবে বিচার চাইবো? কার কাছে চাইলে বিচার পাবো। শুধু এটুকু বলতে চাই, তনুর মা হয়ে দেখুন, কেমন কষ্ট লাগে বুঝতে পারবেন।’
কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষার্থী ও নাট্যকর্মী তনুর মরদেহ পাওয়া গিয়েছিল ২০১৬ সালের ২০ মার্চ রাতে কুমিল্লার ময়নামতি সেনানিবাসের একটি কালভার্টের পাশের ঝোপে। এরমধ্যে মামলাটি নানা হাত ঘুরেছে কিন্তু কোনো অগ্রগতি হয়নি, বরং জিজ্ঞাসাবাদেই ঘুরপাক খাচ্ছে মামলার তদন্ত। তনুর বাবা ইয়ার হোসেন সাংবাদিকদের বলেছেন, “গরিব বলে বিচার পাবো না। আমার পরিবারটা শেষ হয়ে গেছে। খেয়ে না খেয়ে মেয়েকে মানুষ করেছি।”
মামলার দীর্ঘসূত্রতার জন্য আসলে এককভাবে কোনো প্রতিষ্ঠান দায়ী নয়। একটি মামলা দায়ের করার পর থেকে বিচার হওয়া পর্যন্ত পুলিশ, আইনজীবী এবং আদালতের সমন্বিত ভূমিকা আছে। দক্ষ এবং পর্যাপ্ত জনবলসহ তদন্ত এবং বিচারব্যবস্থা ঢেলে সাজানো ছাড়া এ থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় নেই বলেই আইনের সঙ্গে জড়িতরা বলেন। বিচারক স্বল্পতাকে মামলাজট বা মামলার দীর্ঘসূত্রতার প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে আইন কমিশন।
শুধু কি তনু একা? আশির দশকের শুরুর দিকে আতিয়া বেগম তার একমাত্র সন্তানকে হারালেন। আতিয়া বেগমের ছেলে রুবেলকে পানিতে ডুবিয়ে মেরেছে গ্রামের প্রভাবশালী এক ব্যক্তির সন্তান, এমন অভিযোগ থাকলেও, এর কোনো বিচার হয়নি। কারণ রুবেল দরিদ্র ঘরের সন্তান। তাই রুবেলের মা আল্লাহর দরবারে বিচার চাইতে চাইতে প্রায় ১০ বছর পর মারা গেছেন।
কিশোরী মেয়ে মোমেনা সাহায্যকারী হিসেবে ঢাকায় কাজ করতে এসেছিল ২০-২৫ বছর আগে। হঠাৎ ওর বাবা ওকে নিয়ে গেলেন বিয়ে দেবেন বলে। পরে জানা গেলো বিয়ে হওয়ার আগেই মেয়েটিকে কে বা কারা ধর্ষণের পর হত্যা করে কাদায় ডুবিয়ে রেখেছিল। মেয়েটির বাবাকেও বিশ্বাস করতে হয়েছিল জিন বা ভূত মেয়েকে হত্যা করেছে। পরে বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনের পক্ষ থেকে অনেকবার বলা হলেও মোমেনার পরিবার বারবার বলেছে আমরা বিচার চাইনা। এতে অনেক ঝামেলা হয়।
বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের ২০১৭-২০২২ সাল পর্যন্ত কৌশলগত পরিকল্পনায় বলা হয়েছে যে, বিচার ব্যবস্থার অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে ঝুলে থাকা বা বিচারাধীন মামলা। তাদের হিসাবে প্রতিনিয়তই এ সংখ্যা বাড়ছে। বিচার প্রার্থীদের অধিকাংশই বলেন, আমাদের তো ধৈর্য হারিয়ে গেছে। আল্লাহ ছাড়া এ বিচার আর কেউ করবে না। এ রকম লাখ লাখ মানুষ বাংলাদেশের বিভিন্ন আদালতে বছরের পর বছর বিচারের আশায় আছেন।
নারী নির্যাতন বিষয়ে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রায় ৭৩ শতাংশ নারী কোনো না কোনো সময় স্বামীর নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। এদের অধিকাংশই মনে করেন ‘মামলার পেছনে কে দৌড়াবে?’ সরকারি-বেসরকারি দুটি গবেষণায় দেখা যায়, দেশে দুই-তৃতীয়াংশ নারী পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হলেও আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার হার মাত্র ৩ শতাংশ। সচেতনতার অভাব, সংসারে টিকে থাকার ইচ্ছা, লোকলজ্জা ও অর্থ খরচের ভয়ে অধিকাংশ নারী থানায় অভিযোগ করেন না। পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০ অথবা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (সংশোধিত ২০০৩ ও ২০২০) বা অন্য কোনো প্রাসঙ্গিক আইনে তারা বিচার চান না।
মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাধবিজ্ঞান ও পুলিশবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান মুহাম্মদ উমর ফারুক ২০২০ সালে ‘ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেম স্ট্যাটাস কো অ্যান্ড রিকমেন্ডেশন ফর ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স ভিকটিম ইন বাংলাদেশ’ (ফৌজদারি বিচার পরিস্থিতি ও বাংলাদেশে পারিবারিক সহিংসতা) শীর্ষক গবেষণায় বলেছেন শারীরিক, মানসিক, অর্থনৈতিক ও যৌন এই চার ধরনের পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হন দেশের ৮৭ শতাংশ নারী। এর মধ্যে মাত্র ১ শতাংশ মামলা করেছেন এবং প্রায় ৩ শতাংশ সালিশি বা এনজিওর মাধ্যমে মধ্যস্থতা করেন।
মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের জরিপ অনুযায়ী দেশের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ৯ বছরে ২২ হাজার ৩৮৬ জন নারী ধর্ষণসহ বিভিন্ন নির্যাতনের ঘটনায় চিকিৎসা নিয়েছেন। এ ঘটনাগুলোর বিচারিক প্রক্রিয়ায় দেখা গেছে এসব ঘটনায় মামলা হয়েছে মাত্র ৫ হাজার ৩টি। এরমধ্যে রায় ঘোষণা হয়েছে ৮২০টি, শাস্তি হয়েছে ১০১ জনের। শতকরা হিসাবে রায় ঘোষণার হার ৩ দশমিক ৬৬ এবং সাজা পাওয়ার হার ০ দশমিক ৪৫ শতাংশ। আর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালগুলোতে গড়ে মাত্র শতকরা ৪ ভাগ অপরাধী শাস্তি পায়।
শুধু নারী বিচার পাচ্ছেন না ও বিচার চাইছেন না, তা কিন্তু নয়। পুলিশ সদরদপ্তরের এক হিসাবে দেখা যায়, পুলিশ অভিযোগ প্রমাণ করতে না পারায় ৭৬ শতাংশ মামলার ক্ষেত্রে আসামিরা খালাস পেয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশে গড়ে প্রতিদিন ৫০০ ফৌজদারি মামলা হয়। সিআইডির প্রকাশিত তথ্যে দেখা গেছে, ২০১১ সালে সারাদেশে বিভিন্ন মামলায় ২৪ শতাংশ অপরাধীর সাজা হয়েছে। ৬ শতাংশ মামলার ক্ষেত্রে আসামির বিরুদ্ধে পুলিশ অভিযোগ প্রমাণ করতে পারেনি। তবে ২০০৯ সালে সাজার হার ছিল ২৩ শতাংশ। এ সময় পুলিশ তদন্ত করে ৪১ শতাংশ মামলায় অভিযোগপত্র দিয়েছে। বাকি মামলার আসামিরা তদন্ত পর্যায়েই অব্যাহতি পেয়েছে।
অপহরণ মামলার ক্ষেত্রে এই চিত্র আরও ভয়াবহ। দেখা গেছে, গত ২৫ বছরে নিষ্পত্তি হওয়া ২১২ অপহরণ মামলার মধ্যে ১৯০ মামলায় খালাস পেয়েছে আসামিরা; সাজা হয়েছে মাত্র ২১ মামলায়। ৯০ শতাংশ আসামিই এসব মামলায় খালাস পেয়েছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের হিসাব মতে, গত ১৫ বছরে তাদের মামলায় দুই-তৃতীয়াংশ আসামি খালাস পেয়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশনের মামলারও একই অবস্থা। অধিকাংশ মামলায় আসামিরা খালাস পেয়ে যান।
দেশের উচ্চ ও নিম্ন আদালতে ১৫ বছরের ব্যবধানে বিচারাধীন মামলার জট দ্বিগুণ হয়েছে। আইন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির বৈঠকে আইন কমিশনের প্রতিবেদনে এ তথ্য তুলে ধরা হয়। প্রতিবেদন অনুসারে, দেশের আদালতগুলোতে ৪০ লাখের বেশি মামলা ঝুলছে। এর প্রধান কারণ বিচারকের স্বল্পতা। দেশে ৯৪ হাজার ৪৪৪ জনের বিপরীতে বিচারকের সংখ্যা একজন। এই অস্বাভাবিক মামলার জট নিরসনের ব্যাপারে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হলে বিচারব্যবস্থার ওপর সাধারণ মানুষের শুধু আস্থাই হারিয়ে যাবে না; বিচারব্যবস্থাই ভেঙে পড়ার উপক্রম হবে বলে উল্লেখ করা হয় প্রতিবেদনে। হত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতন এবং জমিজমা নিয়ে বহু ধরনের মামলার কাজ বছরের পর বছর ধরে চলছে।
যদি প্রশ্ন করি এ দুরবস্থা কেন? বেশ কিছু কারণ আছে এর পেছনে। অনেক মামলা প্রমাণের জন্য প্রয়োজনীয় সাক্ষ্যপ্রমাণ আদালতে হাজির করতে পারে না পুলিশ। মামলার তদন্তেও ত্রুটি থাকে এবং এর সুবিধা পায় আসামিপক্ষ। আইনের ভাষায় ‘বেনিফিট অব ডাউট’ আসামিদের বাঁচিয়ে দেয়। কারণ বাংলাদেশে ফৌজদারি মামলা সন্দেহাতীতভাবে সাক্ষী প্রমাণের ভিত্তিতে উপস্থাপন করতে হয়।
এছাড়া বিচারহীনতার আরও কিছু কারণ আছে। এর মধ্যে আছে রাজনৈতিক এবং ক্ষমতার প্রভাব, দুর্নীতি, মামলার তদন্তে অদক্ষতা, অপরাধ দমন, তদন্ত এবং বিচারিক প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত জনবলের অভাব। সঠিক তদন্ত হয় না, অনেক মামলায় শেষ পর্যন্ত সাক্ষী পাওয়া যায় না। কারণ অনেক সময় প্রভাবশালী বা সন্ত্রাসীদের ভয়ে সাক্ষীরা আসেন না। এমনকি সাক্ষীদের টাকার বিনিময়ে কিনে নেওয়া হয়। এছাড়া জনবল, অবকাঠামোর অভাব আছে। সাক্ষীদের সুরক্ষা নেই।
বাংলাদেশে নির্যাতনের শিকার ব্যক্তি বা ভিকটিম এবং সাক্ষী বা উইটনেসের সুরক্ষা পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং এর ওপর ভিত্তি করে একটি “ভিকটিম অ্যান্ড উইটনেস প্রটেকশন অ্যাক্ট” প্রণয়নে সহায়তা করার জন্য এমজেএফ ২০২০ সালে যে গবেষণা করেছিল, তাতে বলা হয়েছে ভিকটিমদের জন্য অর্থনৈতিক সহায়তা সবচেয়ে বেশি দরকার। কারণ অধিকাংশ ভিকটিম দরিদ্র এবং দিনমজুর।
কাজেই তাদের পক্ষে আদালতে উপস্থিত থাকার মতো যাতায়াত খরচ ও খাবার কিনে খাওয়ার টাকা থাকে না। ভিকটিমরা সামাজিক নিরাপত্তা চান, যেন তারা স্থানীয় আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মারফত হয়রানির শিকার না হন। বাংলাদেশে এখন এমন কোনো আইন নেই, যা দিয়ে ভিকটিম অথবা সাক্ষীকে রক্ষা করা যায়। এমনকি ভিকটিম এবং উইটনেস কী বা কারা? এ সম্বন্ধে আইনে কোনো সংজ্ঞাও নেই।
সাক্ষীকে বলা হয় বিচারব্যবস্থার কান ও চোখ। আইনকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য বিচারক, পুলিশ এবং তদন্তকারী দলের সামনে ভয়শূন্যভাবে সাক্ষ্য দেওয়াটা অপরিহার্য। দেখা যায় শুধু সাক্ষীকে যথাযথভাবে সুরক্ষার ব্যবস্থা দিতে না পারার ফলে তারা নিজেদের ও পরিবারের জানমাল বাঁচানোর জন্য আসামী পক্ষে চলে যায়।
দলিত-হরিজন জনগোষ্ঠী, হিজড়া, যৌনকর্মী, প্রতিবন্ধী মানুষ, আদিবাসী, ধর্ষণের শিকার নারী ও শিশু সবসময় এ সুরক্ষা আইনের অভাব বোধ করেন। ধর্ষণের মামলায়, মানবপাচার, মাদক চোরাচালান, সন্ত্রাস, মানবতাবিরোধী অপরাধ এসব মামলার যারা ভিকটিম ও সাক্ষী তারাই সবচেয়ে বেশি ভুক্তভোগী হয়ে থাকেন। গবেষণায় দেখা গেছে “ভিকটিম ও সাক্ষীকে সুরক্ষা দেওয়ার মতো কোনো আইন” বাংলাদেশে নেই।
জনসাধারণের মধ্যে আরেকটি কথা প্রচলিত আছে যে বিচার পায় ধনী লোক। টাকা থাকলে, ক্ষমতাবান হলে ও খুঁটির জোর থাকলে মানুষ বিচার পাবে, নয়তো নয়। কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়। আমাদের দেশে দরিদ্র ও ক্ষমতাহীন মানুষ বিচার পায় না, এরকম একটা ধারণা প্রচলিত আছে। কারণ বিচার পেতে চাইলে অনেকটা সময় যেমন অপেক্ষা করতে হয়, তেমনি অনেক টাকাও খরচ হয়। অধিকাংশ পরিবারের পক্ষে এত টাকা ব্যয় করে মামলা চালিয়ে যাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। বিচারহীনতা অবশ্যই অপরাধ বাড়ায়, অপরাধীকে বেপরোয়া করে। এই সংস্কৃতি বন্ধ করতে হবে।
মামলার দীর্ঘসূত্রতার জন্য আসলে এককভাবে কোনো প্রতিষ্ঠান দায়ী নয়। একটি মামলা দায়ের করার পর থেকে বিচার হওয়া পর্যন্ত পুলিশ, আইনজীবী এবং আদালতের সমন্বিত ভূমিকা আছে। দক্ষ এবং পর্যাপ্ত জনবলসহ তদন্ত এবং বিচারব্যবস্থা ঢেলে সাজানো ছাড়া এ থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় নেই বলেই আইনের সঙ্গে জড়িতরা বলেন। বিচারক-স্বল্পতাকে মামলাজট বা মামলার দীর্ঘসূত্রতার প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে আইন কমিশন।
মামলা জটের অন্যতম একটি কারণ হিসেবে প্রয়োজনীয় জনবলের অভাবের কথাও উঠে এসেছে। তারা এও মনে করেন অধিকাংশ মামলার বিচারের ক্ষেত্রেই সময়ের প্রয়োজন। মামলার জাজমেন্ট, সাক্ষীর জেরা ও মামলার রায় লিখতে অনেকটা সময় লাগে। পুলিশও বলেছে মামলার ভারে তারাও জর্জরিত। অপরাধের হার এবং জনসংখ্যার তুলনায় পুলিশের সংখ্যা অনেক কম।
এছাড়া স্থানীয় সরকারের জনপ্রতিনিধিদের ভূমিকা ভিকটিমদের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। তারা ভিকটিমদের সহয়োগিতা করেন না, উপরন্তু ভিকটিমদের হুমকি দেন। তাছাড়া ভিকটিমরা তাদের আইনগত অধিকার সম্পর্কেও জানেন না। অন্য কারণগুলো হলো মামলা সুষম বণ্টন না হওয়া, প্রশাসনিক শৈথিল্য, পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ না হওয়া, কর্মকর্তা-কর্মচারীর জবাবদিহির অভাব, আইনজীবীর আন্তরিকতার অভাব, দুর্বল মামলা ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি।
ভিকটিমদের পরিবার ও অভিভাবকরা যখন বলেন, সন্তান হত্যার বিচার চাই না, মামলা চালানোর মতো অবস্থাও আমাদের নেই, আমরা নিরীহ মানুষ, বিচার চাইলে আল্লাহর কাছে চাই, তিনিই বিচার করবেন- তখন বুঝতে হবে অপরাধীদের নিষ্কৃতি পাওয়ার পথ সুগম হয়েছে বা হচ্ছে। দিনের পর দিন যদি অপরাধীরা শাস্তি না পায় বা শাস্তি পাওয়ার হার খুবই সামান্য হয়, তাহলে অপরাধীরা ভালোভাবেই বুঝে যায় মানুষ অসহায়। অন্যদিকে যারা ভিকটিম তারাও ভয়ের মধ্যে থাকেন। সাধারণ মানুষের মনের এই ভয় যে বঞ্চনা, ক্ষোভ ও হতাশা তৈরি করে, তাতে মানুষ বিচারব্যবস্থার প্রতি আস্থা হারাতে বাধ্য হন।
(তথ্যসূত্র: গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন)
১৭ মার্চ, ২০২৪
লেখক: যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ ও কলাম লেখক।